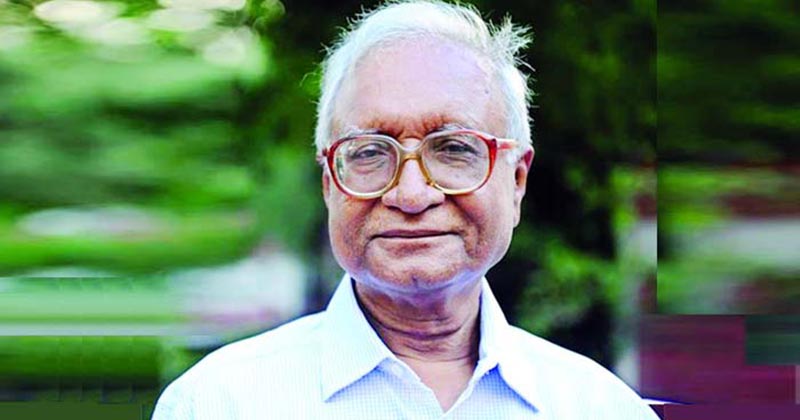না, নির্বাচন মানেই যে গণতন্ত্র, নির্বাচিত সরকার মানেই যে গণতান্ত্রিক- এমন কথা কেউ বলবে না, বলবার উপায় নেই। নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্র খুবই সম্ভব ঘটনা এবং এমন স্বৈরতন্ত্র নিজেকে বৈধ বলে বিশ্বাস করে দাম্ভিকতায় অনির্বাচিত ছিলেন না। হ্যাঁ, গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন দরকার কিন্তু নির্বাচনের আভা দেখেই গণতান্ত্রিক সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা করাটা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। গণতন্ত্রের জন্য আরও অনেক কিছু দরকার।
সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, সেটাকে বুঝতে ও চিনতে হলে অর্ধসত্য দ্বারা বিভ্রান্ত হব না, এ রকমের একটি মনোভাব আবশ্যক। আর এই যে অত্যাবশ্যক উপাদানটাকে চিহ্নিত করা, সে কাজ মোটেই জটিল থাকবে না, বরঞ্চ খুবই সরল ও সহজ হয়ে যাবে যদি গণতন্ত্র জিনিসটা কী, সেটা পরিষ্কার করে নিই। একেবারেই অল্প কথায় বলতে গেলে বলা যাবে গণতন্ত্র হলো সেই রকমের ব্যবস্থা যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার ও সুযোগের সাম্য রয়েছে।
কেবল অধিকার নয়, সুযোগেরও। এর বিকল্প নেই। সমান অধিকারের কথা সংবিধানে লেখা থাকলে চলবে না, তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে হবে। গণতন্ত্র কেবল রাষ্ট্রের ব্যাপার নয়, সমাজেরও ব্যাপার বৈকি। অধিকার ও সুযোগের সাম্য যদি সমাজে না থাকে, তবে রাষ্ট্রে তাকে পাওয়া যাবে না, আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে, তারা যদি সাম্যের ওই আদর্শে বিশ্বাসী না হয়, তারা যদি লালনপালন ও প্রয়োগ ঘটায় বৈষম্যের, তাহলে সমাজে সাম্য থাকবে না। কেননা রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরের অনুপ্রবিষ্ঠ বৈকি।
গণতন্ত্রের জন্য অনেক কিছু চাই। কিন্তু অন্য সবই হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গণতন্ত্রের প্রাণ থাকে ওই এক জায়গাতেই, আর সেটা হলো সাম্য। সাম্য যেখানে যত কম, গণতন্ত্রের পথঘাট সেখানে বিঘ্নসঙ্কুল। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি তাতে বহু ও নানাবিধ উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ওটাই মেরুদণ্ড, যেটা না থাকলে অন্য সবকিছু ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য তা যেমন ভাবেই তাদেরকে জড়ো করা এবং সাজানো হোক না কেন। আর এই যে সাম্য তা কোনো এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, একে ব্যাপ্ত হতে হবে সর্বত্র।
রাষ্ট্রে এবং সমাজে তো বটেই, পরিবারেও। গণতন্ত্র এক ও অবিভাজ্য, তাকে টুকরো টুকরো করা যায় না কিংবা আলাদা আলাদাভাবে যে পাওয়া যাবে, তাও নয়। গণতন্ত্রের এমন বিবরণ শুনলে মনে হতে পারে কোনো কল্পলোকের কথা বলেছি বুঝি। তা প্রকৃত গণতন্ত্র একটা আদর্শ বটে এবং তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমাতে হবে বৈকি। বৈষম্য যত কমেছে গণতন্ত্রও তত এগিয়ে আসবে। উল্টোটা করলে ঘটবে বিপরীত ঘটনা।
বাংলাদেশে আমরা যে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র পাচ্ছি না, তার আসল কারণ হলো এই যে, এখানে বৈষম্য কমছে না, উল্টো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈষম্য বৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রে আগমন-সম্ভাবনা যে পরস্পরবিরোধী, তা প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের যেসব বিজ্ঞ বন্ধু বলেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে যদি সদিচ্ছা থাকে, তারা কার সদিচ্ছার কথা ভাবছেন, সেটা পরিষ্কার হয় না। ভোটারদের সদিচ্ছার ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই, তারা তো চাইবেনই যথার্থ প্রতিনিধি নির্বাচন করতে। সমস্যা হচ্ছে ভোটপ্রার্থীদের নিয়ে। গন্ডগোল এরাই পাকান।
জনগণের কাছে তো তেমন কোনো পছন্দই থাকে না; দুজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয়, যে দুজনের কারও প্রতি ভোটারদের কোনো আস্থা নেই। তারা জানেন এই প্রার্থীরা এখন এসেছেন ভোট চাইতে, জিতলে পরে এদের দেখা পাওয়া যাবে না। যাদের দেখা যাবে, তারা এদের চেলা এবং সেই চেলাদের কাজ হবে জুলুম করা। প্রার্থীরা প্রার্থী হয়েছেন জনগণের সেবা করবার নির্মল আদর্শবোধ থেকে নয়, ক্ষমতা ও টাকা দুটোই লাভ করবেন এই আশায়।
ভোটযুদ্ধ আসলে টাকার যুদ্ধ, তার চেয়ে কম কিছু নয়, বেশিও কিছু নয়। ভয়ংকর এই যুদ্ধে সদিচ্ছার জন্য কোনো জায়গা-জমিন খোলা নেই, এখানে সবটাই বদিচ্ছা। কোটিপতি না হলে এই যুদ্ধে কেউ নামতে সাহস পান না, জেতা তো অনেক দূরের কথা। আর ওই যে যারা কোটিপতি হয়েছেন তারা এমনি এমনি ওটা হননি, হয়েছেন মানুষকে বঞ্চিত করে। গণতন্ত্র এখানে বঞ্চিত জনগণের অধিকার নয়, কোটিপতির ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পত্তি বটে। ধনবৈষম্যের বাস্তবতা বাংলাদেশের নির্বাচনে যেমন নির্লজ্জভাবে নিজেরাই উন্মোচিত হয়ে পড়ে, তেমনটা অন্য কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় না।
এই যে ধনী ব্যক্তিরা যারা নির্বাচনে দাঁড়ান, তাদের কেউ নির্বাচিত হন, কেউ হন না; যারা হন তারা উল্লাস করেন। যারা হন না, তারা নির্বাচিতদের টেনে নামানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা একদলের লোক নয়, কিন্তু একশ্রেণির লোক বটে। আর সেটি হচ্ছে দেশের শাসকশ্রেণি।
শাসকশ্রেণিই শাসন করে অন্যরা সেখানে ঢুকতে পারেন না। এই শ্রেণি এ দলে-ও দলে বিভক্ত, তাদের রাজনৈতিক পোশাক আলাদা, আওয়াজ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আসলে সবাই তারা এক, তারা শাসক আর দেশে রাজনীতির যে মূলধারা, তার সঙ্গে গণতন্ত্রের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, পুরোপুরি সম্পর্ক রয়েছে ক্ষমতা নিয়ে কামড়াকামড়ির। ওই যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সেটাই হলো রাজনীতির প্রধান চেহারা। এই লোকগুলোর হাতেই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে দেশের গণমাধ্যমের : যেজন্য এদের স্ফীত ছবি এবং বিশ্রী বক্তব্য প্রতিনিয়ত আমাদের শুনতে হয়। মনে হয় এরাই বীর, এরাই নায়ক।
বাংলাদেশের সামনে এখন নানা সমস্যা। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক, বেকারত্ব, বিনিয়োগের অভাব সবকিছু মস্ত মস্ত সমস্যা বটে। কিন্তু দেশের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে এর শাসকশ্রেণি। এই শ্রেণির অনুসারীরা লুণ্ঠন করেন এবং ক্রমাগত ধন বৃদ্ধি ঘটান, এদের কীর্তিকলাপেই অন্য সব সমস্যা তৈরি হয়। উৎস অভিন্ন, প্রকাশটাই যা বৈচিত্র্যপূর্ণ। এমন কয়েকটি ঘটনা সর্বসাম্প্রতিকও সংবাদমাধ্যমে উঠে এলো।
গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধক যে বৈষম্য দেশের শাসকশ্রেণি তার যেমন প্রতিনিধি, তেমনি রক্ষাকর্তা। ওই বৈষম্যের ওপর ভর করেই আমাদের শাসকশ্রেণি দাঁড়িয়ে আছে এবং স্বভাবতই তাকে প্রাণপণে রক্ষা করেছে। নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া-ফ্যাসাদ থাকুক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করার ব্যাপারে তারা ভয়ংকর রকমের আদর্শবাদী এবং পরিপূর্ণভাবে আন্তরিক। তাদের তৎপরতা অবিভাজ্য।
স্বাধীনতা এলেও গণতন্ত্রের কিন্তু খবর নেই। খবর না থাকার কারণ তো বোঝাই যায়। সেটা হলো এই যে, পুরাতন শাসকরা চলে গেছেন, কিন্তু তার জায়গায় নতুন যারা এসেছেন তারা ওই আগের শাসকদের মতোই। দৃষ্টিভঙ্গিতে পুঁজিবাদী, আচরণে নিপীড়নকারী। শাসক বদলেছে, শাসন বদলায়নি; হাকিম গেছে, হুকুম রেখে গেছে পেছনে। এই শাসকশ্রেণি পুরাতন বৈষম্য কেবল যে টিকিয়ে রেখেছেন তা নয়, তাকে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তুলেছেন।
এমন অবস্থার ভেতরে বিজ্ঞলোকেরা যখন বলেন যে, নির্বাচনব্যবস্থায় সংস্কার, সিভিল সোসাইটির সক্রিয় ভূমিকা, ক্ষুদ্রঋণের বিস্তার, এনজিওদের কর্মকাণ্ডের প্রসার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্র আনবেন, তখন তাদের সরলতা দেখে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যেতে হয়। এরা কি বোঝেন না যে আসল সমস্যা হচ্ছে সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই, দারিদ্র্য মানুষকে যা নিরাশ্রয় করছে, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে করে তুলেছে বিচ্ছিন্ন ও ভোগবাদী, প্রসার ঘটাচ্ছে মৌলবাদের এবং নিরন্তর বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে বৈষম্যের? এরা যদি না বোঝেন, তবে কে বুঝবে? নাকি বুঝতে চান না, অথবা এমনকি হতে পারে বোঝেন ঠিকই তবে বলেন না, কোন উদ্দেশ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে নিজেদের স্বার্থেই তার আয়োজন ঘটানো? এক্ষেত্রে সত্য এক হোক কিংবা একাধিক হোক, ভীতিজনক বটে। কেননা বিজ্ঞরা যদি অন্ধ হন, তবে সত্যের উন্মোচন কার কাছ থেকে আশা করা যাবে?
তা হলে উপায় কী? উপায় হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা। সেটা যে নির্বাচনের মধ্যে সম্ভব নয়, তাও পরিষ্কার। পথ হচ্ছে আন্দোলন। তা আন্দোলন তো কিছু কম হয়নি। আমাদের দেশেও হয়েছে। বিস্তর আন্দোলন করেছি, প্রাণ দিয়েছি, আশা করছি কিন্তু পূরণ ঘটেনি আশার। এর কারণ রয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ হলো এই যে, আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সীমিত; সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে পরিবর্তন আনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন হয়নি। ফলে পরিবর্তন নিশ্চয়ই এসেছে, রাষ্ট্রের চেহারায় ‘বৈপ্লবিক’ রদবদল পর্যন্ত ঘটে গেছে; কিন্তু সমাজে বৈষম্য তো কমেইনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, তবে গণতন্ত্র যে পাইনি, সেটা একেবারেই নিশ্চিত।
গণতন্ত্রের পথঘাট যে মোটেই মসৃণ নয়, বরঞ্চ আগাগোড়াই এবড়োখেবড়ো এবং বিঘ্নসঙ্কুল; সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে! পৃথিবীজুড়ে মানুষ সেটা বুঝতে পারছে, বুঝতে হচ্ছে আমাদেরও। কিন্তু আসল সমস্যাটা কী? সেটা কোথায়? গণতন্ত্রের জন্য এত যে আকাঙ্ক্ষা, তাকে আনবার ব্যাপারে এমন যে সাধ্য সাধনা, তবু গণতন্ত্র আসে না কেন? প্রয়োজন তাই বৈষম্য নিরসনের, তথা সমাজ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন। এ আন্দোলন জাতীয়তাবাদীরা করেন না, করবেন না; এটি করবার দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্রীদের। তারাই করবেন, যদি কেউ করেন। তেমন আন্দোলনের ফলেই সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন আনা সম্ভবপর। এর কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের পথঘাট অমসৃণই রয়ে যাবে সমাজে যদি মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, যদি না সাম্য আসে অধিকার ও সুযোগের।
লেখক : শিক্ষাবিদ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়